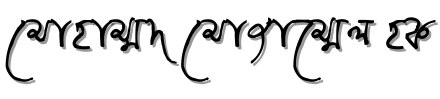আমরা যখন কোনো ঘটনা বা বিষয়ের কারণ জানতে চাই তখন অনেক সময় ভুলে যাই, আসলে ‘আসল কারণ’টা আমরা আদৌ জানতে পারি কিনা। সামগ্রিক বিবেচনায় কোনো কিছুর প্রকৃত সত্যকে জানতে পারাই হলো ‘আসল কারণ’ জানতে পারা। সমস্যা হলো, কোনো কিছু সম্পর্কে কতটুকু জানলে আমরা বলতে পারব, আমরা সবটুকু জেনেছি? কোন প্রেক্ষাপট থেকে কে জানতে চাচ্ছে, তা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।
গঠনগত বা সত্তাগত সীমাবদ্ধতা আমাদের জ্ঞানগত সীমাবদ্ধতার উদ্ভব ঘটায়। গতকাল কোথাও পড়লাম, ডলফিন ১৬০ কিলোহার্টজ পর্যন্ত শব্দ শুনতে পারে। অন্যদিকে, কোনো বাস্তব শব্দতরঙ্গ ২০ হার্ট্জ হতে ২০ কিলোহার্টজের ভিতরে না হলে মানুষ ‘যুক্তিসঙ্গতভাবে’ মনে করতে পারে, ‘কই, না তো! এখানে কোনো শব্দ নাই।’ এবার বুঝেন…! এর সাথে আরো আছে শ্রবণযোগ্য শব্দগুলোর অর্থ বুঝতে না পারার সমস্যা। এই মুহূর্তে আমি গুগল ভয়েস কমান্ড দিয়ে এই লেখাটি লিখছি। বাংলা ভাষা যে জানে না, তার কাছে আমার এইসব কমান্ড নিছক পাখির কিচিরমিচিরের মতো অর্থহীন ধ্বনি।
ইন্দ্রিয়জ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে শুরু করে এভাবে আমাদের জ্ঞানের উৎস ও উপায় মাত্রই স্বীয় গঠনগত কারণে সীমিত বা delimited by its very inner construction।
তাই যখন আমরা কোনো কিছুর সঠিক কারণ জানতে চাই, তখন আসলে সংশ্লিষ্ট বিষয়টিকে আমরা আমাদের মতো করেই জানতে চাই বা জানতে পারি। প্রশ্নকারীকে আমার মতো করে জবাব দেবো, নাকি সে যেভাবে বুঝবে সেভাবে বলবো? এই প্রশ্নের উত্তরে যদি বলেন– বিষয়টা যা বা যতটুকু, আমার উচিত তার সবটুকু খোলাসা করে বলা; তাহলে সমস্যা হলো, প্রশ্নকর্তা physically, metaphysically এবং cognitively আমার সমকক্ষ বা সমপর্যায়ের না হলে যুক্তিসঙ্গত কারণেই তিনি আমার সঠিক উত্তরটিকে ভুল মনে করবেন।
এ কারণে সমকালীন জ্ঞানতাত্ত্বিকদের কারো কারো মতে, জ্ঞান ও যাচাইকরণের ক্ষেত্রে ঔচিত্যবোধ বা sense of duty-কে মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করা উচিত। এটিকে বলা হয় deontological justification। যেমন এক গ্লাস পানিকে রসায়নবিদ্যার ল্যাবরেটরিতে যা বলা হবে সেখানকার জন্য সেটাই সঠিক। যদিও অন্যরা তা বুঝবে না। সবাই সবকিছু না বুঝাটা আদৌ কোনো সমস্যা নয়। বরং সবাই সবকিছু বুঝতে চাওয়ার বা বুঝতে পারার দাবি করাটাই ভুল বা সমস্যার কারণ। কোনো সায়েন্স ল্যাবরেটরির বিশেষ কোনো যন্ত্রকে গুহামানব হয়তো বলবে, এটি একটা জিনিস। অন্যদিকে, আমাদের কাছে এটি একটা মেশিন। ওই ল্যাবের টেকনিশিয়ান যন্ত্রটিকে ব্যবহার করতে জানেন বটে। তবে তিনি বড়জোর এর রিডিং বা ডাটাগুলো নিতে পারেন। শুধুমাত্র গবেষকই পারেন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ওই মেশিন ব্যবহার করে ‘সঠিক জ্ঞান’ অর্জন করতে।
তাই সঠিক জ্ঞান অর্জন করার জন্য উপযুক্ত হওয়া জরুরী। আমরা যে সকল বিষয়ে সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে পারি না, যুক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে আমরা তা বুঝতে পারি। সেজন্য প্রাত্যহিক জীবন থেকে শুরু করে সব বিষয়ে আমরা অন্যদের উপর নির্ভর করি। যেমন গাড়িতে উঠে ড্রাইভারের পেছনে আমরা নিশ্চিন্তে বসে থাকি। ডাক্তারের কাছে গিয়ে নিশ্চিন্ত মনে তার প্রেসক্রিপশনের জন্য বসে থাকি। অনেক আগে বলেছিলাম, we have to believe to live, no matter what we believe!
জ্ঞানের ক্ষেত্রে এই পারস্পরিক নির্ভরতার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য বাস্তবতা। কারো পক্ষে জ্ঞানের জন্য দরকারি সব তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা ও বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয় না। জ্ঞানের জন্য তাই দরকার নলেজ কমিউনিটি। প্রত্যেকটা কমিউনিটির জ্ঞান তাই স্বতন্ত্র।
এই যদি হয় ব্যাপার, তাহলে জ্ঞানের সর্বজনীনতা কীভাবে বজায় থাকে? যারা বলেন ‘জ্ঞানের সার্বজনীনতা বলে কিছু নাই, সব জ্ঞানই আপেক্ষিক’, তারা হতে পারেন এনার্কিস্ট, পোস্ট মডার্নিস্ট। কিন্তু উত্তর-আধুনিকতাবাদীদেরকে বলতে হবে, ‘২+২=৪’ কেন সার্বজনিন সত্য? অথবা, ‘মানুষ মরণশীল’ – এই কথাকে কেন আমরা চিরন্তন সত্য হিসাবে মানি?
তাহলে দেখা যাচ্ছে, সত্তাগত সীমাবদ্ধতার কারণে আমরা সব বিষয়ে সঠিক জ্ঞান ‘সঠিকভাবে’ অর্জন করতে পারি না। অথচ, intuitively বা স্বজ্ঞাবলে আমরা বুঝতে পারি, সঠিক জ্ঞান বা পরিপূর্ণ সত্য বলে কিছু জিনিস আছে। কারণ, আমরা মনে করি ‘সবকিছু আপেক্ষিক’ কথাটা স্বয়ং আপেক্ষিক হতে পারে না। তারমানে, কিছু কিছু বিষয় কিছু কিছু ক্ষেত্রে আপেক্ষিক বটে। তবে সব কিছু সব সময়ে আপেক্ষিক নয়। জগতে চিরন্তন সত্য বলে অবশ্যই কিছু না কিছু আছে। এবং যা ‘আসলেই আছে’ তা জানার আগ্রহ থেকে মানুষ নিজেকে কখনোই নিবৃত করতে পারে না।
জ্ঞানের প্রতি মানুষের এই অনুরাগ অসীম ও অদম্য। এই দৃষ্টিতে জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ বা জ্ঞানতৃষ্ণা হলো মানুষের অন্যতম আদিম প্রবৃত্তি। জ্ঞানের প্রতি অনুরাগের এই সহজাত প্রবণতা মানুষকে পাশবিক স্তর থেকে সভ্যতার স্তরে উপনীত করেছে। নিজের সীমাবদ্ধতার জন্য মানুষ নলেজ কমিউনিটি ডেভলপ করেছে। আমরা জানি, knowledge is a community phenomenon, as like as language। জানার জন্য মানুষ পরস্পরের উপরে নির্ভর করে। একজন আরেকজনকে বিশ্বাস করে। আস্থা রাখে।
আমরা জানি, বস্তুবাদের ভিত্তি হলো অভিজ্ঞতাবাদ। অথচ, কোনো বিষয়ে প্রয়োজনীয় সকল অভিজ্ঞতা কেউ ব্যক্তিগতভাবে অর্জন করতে পারে না। সেজন্য আমরা দেখতে পাই, testimony বা সাক্ষ্য ছাড়া অভিজ্ঞতাবাদ অচল। যদিও জ্ঞানের উৎস হিসেবে empiricism এবং testimony এই দুইটা স্বতন্ত্র। আরেকজনের অভিজ্ঞতাকে যদি আমি নিজের অভিজ্ঞতা হিসেবে গ্রহণ না করি তাহলে আমাদের জন্য জ্ঞান অর্জন অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। এর পরিণতি হলো চরম আত্মকেন্দ্রিকতাবাদ বা solipsism। জীবন ও জগতের প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত ও জ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে আমার-আপনার ব্যক্তিগত সক্ষমতার রয়েছে সীমাবদ্ধতা। এর বিপরীতে, আরেকজনের অভিজ্ঞতাকে যখন আমরা নিজেদের অভিজ্ঞতা হিসেবে গ্রহণ করি তখন একদৃষ্টিতে আমরা একটা হাস্যকর কাজে লিপ্ত হই।
আপনার হাঁটুতে আমি ব্যথা অনুভব করতে পারি না। আপনার ব্যথায় আমি সমবেদনা জানাতে পারি বড়জোর। যতই ভালোবাসা থাকুক, আমি খেলে আপনার পেট তো আর ভরবে না। তাই না? তাহলে আপনার অভিজ্ঞতা কেন আমাকে satisfy করবে? জ্ঞান দান করবে?
অভিজ্ঞতাকে জ্ঞানের উৎস হিসেবে গ্রহণ করার এই উভয় সংকট নিয়েই আমাদের তাবৎ জ্ঞানচর্চা ও জ্ঞানযাত্রা। অভিজ্ঞতার বাইরে বিশ্বাস ও আস্থার ব্যাপারটা তাই সবিশেষ গুরুত্ববহ।
সঠিক জ্ঞানের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি বা সত্তার ওপর নির্ভর করতে হয়। তাই বলে কোনোও অবস্থাতেই অন্ধবিশ্বাসী হওয়া যাবে না। অন্ধবিশ্বাস এবং সঠিক বিশ্বাসের মধ্যে পার্থক্য হলো, অন্ধবিশ্বাসের ক্ষেত্রে মানুষ নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বিষয়কে যাচাই বাছাই করা ছাড়াই whimsically কারও ওপর আস্থা জ্ঞাপন করে। এর বিপরীত কোনো কথা বা যুক্তি সে শুনতে নারাজ। অপরদিকে, একজন নিষ্ঠাবান অনুসন্ধানী কোনো কমপিটেন্ট ও সিনসিয়ার গাইডের উপর নির্ভর করে। সব ক্ষেত্রে সবার জন্যই এটি সঠিক পদ্ধতি। এ ধরনের বিশেষজ্ঞ বা আস্থাযোগ্য গাইডকে আমরা দৃশ্যত অন্ধ-অনুসরণ করলেও প্রকৃতপক্ষে তা অন্ধবিশ্বাস নয়। বরং তা আমাদের যুক্তিবুদ্ধিরই দাবি।
যে কোনো বিষয় বা পরিস্থিতিতে আমাদের উচিত নিজ নিজ অভিজ্ঞতা, যুক্তি, বুদ্ধি ও সামর্থ্যকে সর্বোচ্চ কাজে লাগানো। এ ধরনের অনুসন্ধিৎসু মন-মানসিকতা সবসময় বজায় থাকতে হবে। একই সাথে এটিও স্মরণে রাখতে হবে, আমাদের শারীরিক, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতার রয়েছে সুস্পষ্ট সীমাবদ্ধতা। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উপযুক্ত অথরিটির পরামর্শ ও গাইডলাইনকে তাই যথাযথভাবে মেনে চলা জরুরি। তাহলেই কেবল আমরা কোনো কিছুর কারণ যথাসম্ভব সঠিকভাবে জানতে পারবো।
সব বিষয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সাধারণত আমরা এটা করে থাকি। এতে কোনো সমস্যাবোধ না করলেও জীবন ও জগতের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও সম্ভাব্য কোনো অন্তর্নিহিত কারণ বা যুক্তি থাকা, না থাকা সংক্রান্ত মৌলিক বিষয়গুলো ডিল করতে গিয়ে সংশয়বাদী ও বস্তুবাদীরা নানা ধরনের ভুল প্রশ্ন বা ক্যাটাগরি মিসটেক করে থাকে।
‘ঈশ্বর কেন আছেন? কেন তিনি জগৎ সৃষ্টি করেছেন? কেন তিনি জগতকে এভাবে সৃষ্টি করেছেন?’ – এ ধরনের প্রশ্নগুলোর সমস্যা কোথায়, কিম্বা এ ধরনের প্রশ্নগুলোকে কীভাবে রেসপন্স করা উচিত, সম্মানিত পাঠক এতক্ষণে নিশ্চয়ই তা বুঝে ফেলেছেন।
গতকাল এক তরুণ ফেসবুক বন্ধু ইনবক্সে প্রশ্ন করেছেন, ‘ঈশ্বর কেন জগৎ সৃষ্টি করেছেন?’ প্রথমে আমি কিছুটা বিরক্ত হয়ে স্রেফ ‘জানি না’ বলে শেষ করেছিলাম। পরে সেই প্রশ্নের বিস্তারিত উত্তর দিয়েছি। আলোচনার শেষের দিকে জানতে পারলাম, তিনি প্রশ্নটা করেছেন তার ছোট ভাইয়ের বরাতে। তার সেই ভাই ক্লাস নাইনে পড়ে। হাজার বছর ধরে ইসলামিক স্কলারগণ রিচুয়ালিস্টিক প্রসেসে থিওলজি, বিশেষ করে ফিকাহর দৃষ্টিতে মানুষকে ইসলাম সম্পর্কে বলে এসেছেন। এখন সময় এসেছে বা এখনকার যুগের দাবি হলো, যে কোনো কিছুকে যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে উপস্থাপন করার। চাপিয়ে দেওয়ার যুগ শেষ। ইসলাম বা যে কোনো আইডিওলজির জন্য এটি সত্য।
বলেছিলাম, ‘কথা বলতে দিতে হবে, চাই প্রশ্ন করার অধিকার।’ হ্যাঁ, ঠিকই বলেছি। যদিও আমরা জানি, সব প্রশ্ন সঠিক নয়। সব প্রশ্ন উত্তরযোগ্য নয়। অথবা, নয় আমাদের দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ কিংবা অর্থপূর্ণ।
আদর্শ যা-ই হোক না কেন, যারা আদর্শের কথা বলবেন, তাদের দায়িত্ব হলো সবার সব কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা এবং সেগুলোর যথাযথ উত্তর সুন্দর ভাষায় উপস্থাপন করা। উত্থাপিত প্রশ্ন ক্যাটাগরি মিসটেক বা ভুল ধরনের প্রশ্ন হয়ে থাকলে করণীয় হলো প্রশ্নের ভুল কোথায় তা গ্রহণযোগ্য যুক্তি দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া। প্রশ্নকারীদেরও উচিত, জেদাজেদি না করে কোনো কথাকে গ্রহণ করে নেয়া, যদিও সেটা নিজের পূর্ববর্তী মতের বিরুদ্ধে যায়। কথাটা যদি হয় অধিকতর যুক্তিসঙ্গত।